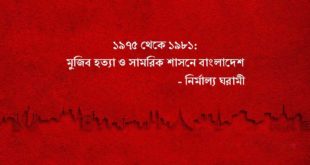রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন অশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ। সারা জীবন তিনি নিরলসভাবে দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন কাজ করে গেছেন, কিন্তু তা করেছেন নীরবে এবং লোকচক্ষুর আড়ালে। নিজের জীবনচর্যায় রথীন্দ্রনাথ বরাবরই পিতা রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। একদা নিজের জন্মদিনে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন — “বাবাকে যত দেখছি ততই কষ্ট হচ্ছে — তিনি অবশ্য কিছু বলেন না – কিন্তু স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনো সুখ নেই। আমার কষ্ট আরও বেশি হয় এই জন্য যে, আমি তাঁকে সুখী করতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি তা হলেই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু।” বিখ্যাত পিতার প্রলম্বিত ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণে হোক বা নিজের নেপথ্যচারী স্বভাবের জন্য হোক — তিনি কখনও পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেননি। হয়তো সেই জন্যই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়নি এবং জনমানসে তিনি সেভাবে রেখাপাত করতে পারেননি।
পিতার বৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রায় সব ব্যবহারিক দিকের দায়িত্বই ন্যস্ত ছিল রথীন্দ্রনাথের উপর। পাশাপাশি তাঁর নিজের প্রতিভারও স্ফূরণ ঘটেছে, তবে তার প্রকাশ নিভৃতে। তাঁর জন্ম ১৮৮৮ সালের ২৭ নভেম্বর, কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কবি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্রকে পল্লীসংস্কারের কাজের জন্য তৈরি করতে। স্কুল ও কলেজের পড়াশোনা শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কবি মনে মনে যে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভেবেছিলেন রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের উন্নত পদ্ধতিতে চায করতে শেখাবেন।
ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসেন এবং পিতার গ্রামোন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি শিলাইদহে একটি কৃষি খামারের পত্তন করেন এবং মৃত্তিকা-বিজ্ঞানে নিজের ব্যুৎপত্তি কাজে লাগিয়ে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য একটি ল্যাবরেটরিও তৈরি করেন। এছাড়া তিনি উন্নত ধরনের লাঙল এবং নানা যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিজে ট্রাক্টর চালিয়ে কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করতে শিখিয়েছিলেন। শিলাইদহে কৃষি-খামারের কাজ ছাড়াও তিনি চাষিদের আলু, টমেটো এবং আখের চাষ করার দিকে উৎসাহিত করেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এলাকায় পিতৃবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আলু চাষের প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি লিখেছেন — “আমাদের দেশে তখনকার দিনে সাধারণের মধ্যে আলু খাওয়ার তেমন প্রচলন হয়নি। আলুর চাষ করতে কৃষকেরা জানত না। দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি একবার এসে আলুর চাষ প্রচলিত করবার জন্য বাবাকে উৎসাহিত করেন। বাগানের একপ্রান্তে আলুর খেত প্রস্তুত করা হল। আলুর চাষের এটাই হবে পরীক্ষাকেন্দ্র। দ্বিজুবাবু বললেন, তিনিই বীজ পাঠিয়ে দেবেন এবং কী করে জমির পাট করতে হবে, কী সার দিতে হবে সব বিষয়ে মালীকে বুঝিয়ে দেবেন।” শিলাইদহ ছাড়া পতিসর এবং কালীগ্রাম পরগণাতেও তাঁর কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল। খুব মুন্সীয়ানার সঙ্গে তিনি কৃষি-বিষয়ক জটিল বিষয় বাংলায় উপস্থাপন করেছেন।
শান্ত, নীরব প্রকৃতির রথীন্দ্রনাথকে দেখলে বোঝা যেত না তিনি কী বিপুল কর্মপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আমেরিকায় থাকাকালীন কিছু বিদেশি ছাত্রকে একত্রিত করে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ‘কসমোপোলিটান ক্লাব’ নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর এই গঠনমূলক প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর কাজের মধ্যে সার্থক রূপ পায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাধের ‘বিচিত্রা’ কলকাতার সমাজে সাহিত্যরুচি গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়ক ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। তিনি উদ্যোগী হয়ে তখনকার সাহিত্য-শিল্প রসিকদের ‘বিচিত্রা’-র সঙ্গে যুক্ত করতেন। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ঠাকুরবাড়িতেও আলোড়ন তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই রথীন্দ্রনাথের উপরেও তার প্রভাব পড়েছিল। দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বদেশী গান গেয়ে ন্যাশনাল ফান্ডের জন্য কিছু টাকা তুলেছিলেন। এছাড়া তিনি কিছু দিন অনুশীলন সমিতিতে জুজুৎসুও শিখেছিলেন।
রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে অগ্রণী হয়ে গগনেন্দ্রনাথের অল্পবয়সী বিধবা ভাগ্নি প্রতিমা দেবীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর বিবাহ হয়। ওই বছরের ২ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে একটি চিঠিতে পুত্রবধূ সম্পর্কে লেখেন — “তাকে মানুষ হিসেবে সমগ্রভাবে তোকে দেখতে হবে — কেবল গৃহিণী এবং ভোগের সঙ্গিনীভাবে নয়। ওর মধ্যে যে বিশেষ শক্তি আছে তার কোনোটা যদি অনাদরে নষ্ট হয় তাহলে ওর সমস্ত প্রকৃতিতে তার আঘাত লাগবে — এই কথা স্মরণ করে কেবলমাত্র নিজের রুচি, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের দিক থেকে প্রতিমাকে দেখলে হবে না — ওর নিজের দিক থেকে ওকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে, এই ভার তোরই উপর।” একইভাবে ১৯১৪ সালে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন — “তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না — প্রতিদিন তার নিত্য নতুন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে দিন, এই আমি কামনা করি।”
১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠান। তখন থেকেই রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি শান্তিনিকেতনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। শান্তিনিকেতনে তখন চরম আর্থিক অস্বাচ্ছল্য চলছিল। সেই কঠিন সময়ে নানা আইনগত সমস্যা ও আর্থিক দুরবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তিনি বৈষয়িক কাজকর্ম পুরোটাই নিজের হাতে তুলে নেন। ১৯২১ সালে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তকুমার মহলানবীশ তার যুগ্ম সচিব হয়েছিলেন। পরে তিনি একাই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ কাজে সুরেন্দ্রনাথ কর ও অনিল চন্দ তাঁর সহযোগী ছিলেন। নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ গড়ে তোলার কাজে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং নিরলস পরিশ্রম করেছেন। কালীমোহন ঘোষের লেখায় এর উল্লেখ আছে।
বিশ্বভারতীয় প্রথম দিকে রথীন্দ্রনাথ কিছুদিন পড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে সে কথা লিখেছেন। বিশ্বভারতীয় বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পাঠভবন নিয়েই তাঁর চিন্তা ছিল সব থেকে বেশি। তিনি এখানে পড়াশোনা করেছিলেন বলেই বোধহয় এই বিভাগের ওপর তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। সর্বশ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি ঘরের ও বাইরের কাজে সহজেই কর্মী তৈরি করতে পারতেন এবং তাদের দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। তিনি সব সময় সহকর্মীদের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন এবং তাঁদের প্রয়োজনে সাহায্যও করতেন। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের সেই অনটনের দিনে দেশি-বিদেশি অতিথিদের আসা-যাওয়া থেকে শুরু করে থাকা-খাওয়া ও আপ্যায়নের যাবতীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। তাঁর অতি ভদ্র ব্যবহার ও সহজাত সৌজন্যের সঙ্গে মিশেছিল উদারতার মাধুর্য। সব কাজই তিনি নীরবে সমাধা করতেন, তাঁকে গলা তুলে কথা বলতে কেউ শোনেনি।
বিশ্বভারতী যেন ছিল রথীন্দ্রনাথের সাধনার অঙ্গ এবং পিতার আদর্শকে রূপায়িত করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে রাজশাহী ডিভিশন থেকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির সদস্য হতে অনুরোধ করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থাও করে রাখেন। রবীন্দ্রনাথ এতে সম্মতি দিলেও তিনি কিন্তু বিশ্বভারতীর কাজ ছেড়ে যেতে রাজী হননি। পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরু তাঁকে রাষ্ট্রদূতের পদ দিয়ে বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর আর্থিক অনটনও ছিল। কিন্তু বিশ্বভারতীর ক্ষতির কথা ভেবে তিনি সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মূল কাজ ছিল বিশ্বভারতীর ভাঙন ঠেকিয়ে রাখা। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে তিনি তার প্রথম উপাচার্য হয়েছিলেন। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল বিশ্বভারতীয় উপাচার্যরূপে প্রথম সমাবর্তনে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। ১৯৫১ সালের ১৪ মে থেকে ১৯৫৩ সালের ২২ আগস্ট পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কবির আশ্রম থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলে যাওয়াটা আসলে এক বিপর্যয়। ক্ষমতার রাজনীতি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারি নিয়মের ঘেরাটোপ।
রথীন্দ্রনাথ প্রায়ই পিতার ভ্রমণ-সঙ্গী হতেন। বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি পিতার সচিবের ভূমিকা পালন করতেন। এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ১৯১২-১৩ সালে লন্ডনে বাসকালে টিউব রেলে ব্লুমসবেরি যাওয়ার সময় কবির একটি সুটকেস খোয়া যায়। এই সুটকেসের ভেতরেই অন্যান্য দরকারী কাগজপত্রের সহ্গে ছিল কবির গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। পরে সুটকেসের খোঁজ পড়লে রবীন্দ্রনাথ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন রথীন্দ্রনাথ রেলের হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র অনুসন্ধানের অফিসে খোঁজ করে সেটি ফেরত নিয়ে আসেন। ‘পিতৃস্মৃতি’-তে তিনি লিখেছেন — “মাঝে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভাবি যদি ইংরেজি গীতাঞ্জলি আমার অমনোযোগ ও গাফিলতির দরুণ সত্যিই হারিয়ে যেত, তাহলে . . .।” তাহলে যে কী হত আমরা তা দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না!
১৯১২ সালে পিতার সঙ্গে লন্ডনে থাকাকালীন রথীন্দ্রনাথ এমন একটি কাজের সূত্রপাত করেছিলেন যার জন্য পরবর্তীকালের রবীন্দ্র-গবেষক তথা পাঠকরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরের কাটিংগুলি তিনি সংগ্রহ করে গুছিয়ে রাখতেন। এগুলি বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ও কাজকর্মের ঐতিহাসিক দলিল বলা চলে। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি পিতার নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির পর থেকে সংগৃহীত কাটিংগুলি তারিখ অনুসারে বিন্যাস করে নিজে লিখে রাখতেন। এ ছাড়া তিনি পিতার সব চিঠিপত্র ও রচনার কপি সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। এই সব মূল্যবান বস্তু এক জায়গায় সংগ্রহ করে তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের দপ্তর স্থাপন করেন। এটি পরে ‘রবীন্দ্রভবন’ নামে পরিচিত হয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসারে রথীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রজীবনীর অনেক অংশ লেখা সহজ হয়েছিল।
বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার পাশাপাশি রথীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল মনও সক্রিয় থেকেছে। চামড়ার কাজে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। ১৯২৬ সালে মিলান থেকে তিনি চামড়ার কাজ শিখে আসেন, কিন্তু নিজে কাজ করার সময় তিনি পুরোপুরি দেশি নকশায় নানান জিনিস তৈরি করতেন। আজ আমরা যে সব চামড়ার ব্যাগকে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ বলে চিনি, তার সূচনা হয়েছিল রথীন্দ্রনাথেরই হাতে। ছাত্রছাত্রীদের এই কাজ শেখানোর জন্য তিনি প্রতিমা দেবীর সঙ্গে মিলে শ্রীনিকেতন শিল্পসদন গড়ে তোলেন। কাঠের কাজেও তাঁর বিশেষ পারদর্শীতা ছিল। তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য হল কাঠে তিনি কোনওরকম রং দিতেন না, বরং নানা রঙের কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলির সাহায্যে তিনি বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর তৈরি কাঠের জিনিসপত্রে শিল্পরুচির পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। তাঁর নিজের কথায় — “জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।” আশেপাশের গ্রামের মানুষজন যাতে কাঠ, চামড়া ইত্যাদির কাজ শিখে স্বনির্ভর হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের হাতে তাদের কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁকে একটি সরকারি শিল্প-সংস্থায় উপদেষ্টা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় — “তাঁর মেজাজটি ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের।”
ঠাকুরবাড়ির শিল্প-প্রতিভার ধারা অনুসরণে রথীন্দ্রনাথও ভারি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। তাঁর আঁকা ছবিতে অন্য কোনও শিল্পীর প্রভাব একেবারেই নেই, তা সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব ধারায়। তাঁর আঁকা অসংখ্য ছবির মধ্যে ফুলের ছবি ও দৃশ্য-চিত্রই বেশি। তাঁর আঁকা ফুলের ছবি এত জীবন্ত যে মনে হয় সত্যিই ফুল ফুটেছে, এগুলির মধ্যে গোলাপ ফুলের ছবিই আবার সব থেকে বেশি খুলেছে। পুত্রের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — “রথীর মতো এত নিপুণ করে আমি ফুলের ছবি আঁকতে পারি না।” ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ দিল্লিতে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয়, যার উদ্বোধন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। চিনদেশ থেকে তাঁকে একটি উপাধি দেওয়া হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে কলকাতায় ও কলাভবনে উৎসব ও প্রদর্শনী হয়। আরও পরে ১৯৫২ সালে কলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে একটি প্রদর্শনী হয়।
রথীন্দ্রনাথের ফুলের ছবির প্রতি অনুরাগ পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল তাঁর উদ্যানপ্রীতিতে। উদ্যানরচনা যে বিজ্ঞানচর্চার অন্তর্গত একটি শিল্প-সাধনা, পরবর্তী ভারতীয় কৃষিবিদেরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁরই দেখানো পথে। দেশ-বিদেশ থেকে আনা বিভিন্ন ধরনের চেনা-অচেনা ফুলগাছের পারস্পরিক মিলন নিয়ে তিনি সারা জীবনই পরীক্ষা চালিয়েছেন। উত্তরায়ণের বাগান তিনি শ্রীময়ী করেছিলেন অসংখ্য গাছ ও লতাপাতা দিয়ে। উত্তরায়ণের বাগানে ছিল বিভিন্ন রকম ফুলের রকমারি সমাবেশ। শান্তিনিকেতনের পাথুরে মাটিতে বিভিন্ন রকমের বহু সংখ্যক গোলাপের চারা লাগিয়ে তিনি একটি সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে তৈরি করেছিলেন আমের বাগান। উদয়ন যাবার মুখে লোহার রেলিং-এর সঙ্গে পেয়ারা, আম, জামরুল, সফেদা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাকে জড়িয়ে তিনি লতানো গাছে পরিবর্তিত করেছিলেন। এখানেই তাঁর তৈরি ‘গুহাঘরে’ বসে তিনি বিশ্বভারতীর যাবতীয় কাজের পাশাপাশি শিল্পচর্চা করে যেতেন। গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা ও রূপদান তাঁর একটা বিশেষ শখ ছিল। রবীন্দ্রনাথ এক বাড়িতে বেশি দিন থাকতে চাইতেন না। তাঁর নতুন বাড়ির সখ মেটাতে সুরেন কর ও নন্দলালের সহযোগিতায় রথীন্দ্রনাথ উদয়ন, কোণার্ক, পুনশ্চ, উদীচী প্রভৃতি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। স্থাপত্যের নক্সার অভিনবত্বে ও বহিরঙ্গের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে এই বাড়িগুলি অনবদ্য। বিশেষত উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়িটির আভ্যন্তরীণ সজ্জায় যে উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।
রথীন্দ্রনাথ ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু অন্তরে সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। দেশি-বিদেশি সাহিত্য তিনি আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় দখল সম্বন্ধে এলমহার্স্ট বলেছিলেন — “এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে চর্চা করলে ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল।” ১৯৫৮ সালে (তাঁর ৭০ বছর বয়সে) প্রকাশিত স্মৃতিমুখর ‘On the Edges of Time’ পড়লে বোঝা যায় এ কথা যথার্থ। ঝরঝরে ইংরেজিতে লেখা এই বইয়ের ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। বস্তুত নিজেকে অন্তরালে রেখে জীবনস্মৃতি লেখার এ এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত বলে পরিগণিত হয়। নানান খুঁটিনাটি তথ্যে সমৃদ্ধ এই বইটি আদ্যন্ত এক ঐতিহাসিক দলিল। পরে এই বইটিই তিনি ‘পিতৃস্মৃতি’ নাম দিয়ে বাংলায় লেখেন। বাংলার এক গৌরবময় যুগের কথা, পিতার কথা ও চারপাশের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের কথা তিনি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখে গেছেন, তবে লিখতে বসে কোথাও নিজেকে জাহির করেননি।
ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায়ও রথীন্দ্রনাথের ভালোই দখল ছিল। অশ্বষোষের ‘বুদ্ধচরিত’ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন। ‘বিচিত্রায়’ তাঁর গল্প ‘বাঁধাঘাট’ (১৯৩৭) প্রকাশিত হয়েছিল। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল ‘একটি ভালুকের গল্প’। তা ছাড়া ‘পুরুষের মন’ (১৯৩৭), ‘বাঙালী মেয়ে’, ‘শেষ দান’ ইত্যাদি কিছু কবিতাও তিনি লেখেন। বাংলায় দু’টি বিজ্ঞানবিষয়ক বইও তিনি লিখেছিলেন — ‘প্রাণতত্ত্ব’ এবং ‘অভিব্যক্তি’। এই বইদু’টির বৈশিষ্ট্য অলংকারবিহীন ও আবেগের আতিশয্যহীন ভাষা, যা বিজ্ঞান রচনার পক্ষে একান্ত উপযোগী। এখানে উল্লেখ্য, এই দু’টি বই-ই তিনি প্রকাশ করেছিলেন পিতার মৃত্যুর পর, যা থেকে মনে হয় লাজুক স্বভাবের ও পিতার প্রতিভায় আচ্ছন্ন পুত্র লেখনীর মাধ্যমে অসংকোচে আত্মপ্রকাশে ভরসা পাননি।
রথীন্দ্রনাথ রুচি ও শিল্পের ছোঁয়ায় বিশ্বভারতীর জীবনযাত্রাকে শিল্পিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সংসারের কাজেও তিনি দক্ষ ছিলেন। জেলি, আচার প্রভৃতি খুব ভালো তৈরি করতেন এবং দই পাততেও পারতেন। তা ছাড়া তিনি সুগন্ধি পাউডার এবং সেন্টও তৈরি করতে পারতেন। শেষের দিকে তিনি কিছু সাজসজ্জার জিনিস বাজারে ছেড়েছিলেন। তাঁর শিকারের নেশা ছিল, প্রায়ই শিকারে যেতেন। আর তাস খেলতে তিনি খুব ভালোবাসতেন, উত্তরায়ণে রোজ সন্ধ্যায় ব্রিজের আড্ডা বসতো। এ সম্পর্কে পিতার বিরক্তি প্রকাশ সত্ত্বেও তিনি তাস খেলা বন্ধ করেননি। তিনি এস্রাজ বাজানোয় দক্ষ ছিলেন এবং পিতার গানও গাইতেন, তবে সকলের সামনে নয়। কেবল ঘনিষ্ঠজনের বৃত্তে তাঁর স্বভাবের এই দিকগুলো প্রকাশ পেত।
শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রথীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ১৯৩৮ সালে বিশ্বভারতীর ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী মীরার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মীরা তাঁর থেকে একত্রিশ বছরের ছোট ছিলেন এবং তাঁর এক কন্যাও বর্তমান ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে চতুর্দিকে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। রথীন্দ্রনাথের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ আসে, একের পর এক কুৎসায় তিনি নাজেহাল হয়ে যান। এমনকী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁদের শান্তিনিকেতন থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। পরিশেষে রাগে ও অভিমানে বিশ্বভারতী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে রথীন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন। তার পর নির্মলচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে মীরা চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেরাদুনে চিরতরে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান। প্রতিমা দেবী শুধু অনুরোধ করেছিলেন যেখানেই থাকুন না কেন ভালো আছেন এই সংবাদটুকু জানাতে। রথীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে চিঠি লিখে সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। দেরাদুনেই ১৯৬১ সালের ৩ জুন তারিখে ৭২ বছর বয়সে চিরকালের নেপথ্যচারী মানুষটির জীবনাবসান হয়। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন — “ইনি বরাবর জীবনের একটি ছন্দ বজায় রেখেছিলেন, মৃত্যুতেও তার ছন্দপতন হয়নি।”
রথীন্দ্রনাথের প্রায় সারাটা জীবনই পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে কেটেছে এবং সে জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকারও করেছেন, সৃজনশীলতায় মগ্ন থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি। পত্নী মৃণালিনী এবং পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু কবিকে যে কতটা দুঃখী করেছিল, তা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই পিতাকে সুখী করাটাই তিনি জীবনের ব্রত বলে হিসেবে নিয়েছিলেন, তাঁর চাওয়াকেই তিনি বরাবর নিজের চাওয়া বলে মেনেছিলেন। পিতার সন্তুষ্টির জন্য তিনি কৃষিবিজ্ঞান পড়েছেন, পরে তাঁরই আহ্বানে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবনের শেষের ক’টি বছর বাদ দিলে সুদীর্ঘকাল তিনি শান্তিনিকেতনে কাজ করেছেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়রূপে পরিচিতি পায় তার পেছনে রথীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রথম উপাচার্য। আমরা যে আজ রবীন্দ্রনাথকে এত ভাবে জানতে পেরেছি তার অন্যতম কারণ তিনিই। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি, যথাযথ মর্যাদাও তিনি পাননি। তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে লোকচক্ষুর আড়ালে। স্নেহশীল পিতা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের বিভিন্ন দিকগুলি তিনি অনুভব করেছিলেন এবং পিতার দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করাই তিনি প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু সেই কর্তব্য পালনের তাগিদে তাঁর শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক মনটি চাপা পড়ে গেছে।
উপসংহারে একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর রথীন্দ্রনাথ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, যাতে রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে’ গানটি জাতীয় সঙ্গীত হয় সে জন্য দরবার করতে। সেই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পরেই তিনি ফিরেছিলেন।
সহায়ক গ্রন্থাবলী : –
১. আপনি তুমি রইলে দূরে : সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রথীন্দ্রনাথ — নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।
২. আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ — রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মশতবর্ষপূর্তি শ্রদ্ধার্ঘ্য — অনাথনাথ দাস সম্পাদিত।
 utoldhara.com সপরিবার বাঙলির মনের ঠিকানা
utoldhara.com সপরিবার বাঙলির মনের ঠিকানা